শিতাংশু ভৌমিক অংকুর,
সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে প্রোপ্যাগান্ডার আগুন জ্বলছে। হাইকোর্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী এক প্রার্থীর প্রার্থিতা নিয়ে রিট শুনানি করে নির্বাচন স্থগিত করার আদেশ দিলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। পরে চেম্বার জজ আদালত সেই স্থগিতাদেশ বাতিল করে দেন, ফলে নির্বাচন অব্যাহত থাকার পথ পরিষ্কার হয়। এই ঘটনা আমাদের দেখাচ্ছে, নির্বাচন শুধু ভোটগ্রহণ নয়; এটি মনস্তাত্ত্বিক লড়াই, তথ্য যুদ্ধ এবং প্রোপ্যাগান্ডার ছড়ানোর এক বৃহৎ মঞ্চ।
বামজোট মনোনীত প্যানেলের প্রার্থী বিএম ফাহমিদা আলম অভিযোগ করেন, ডাকসুর জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ আসলে নিষিদ্ধ সংগঠন ও ছাত্রলীগের নেতা। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই তিনি রিট দায়ের করেন। ফাহমিদার বক্তব্য ছিল স্পষ্ট—তিনি নির্বাচন বন্ধ করতে চান না, বরং ডাকসুর মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ রক্ষায় একজন প্রার্থীর যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ করছেন। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি ভিন্নভাবে প্রচার করা হয়। নানা ফেসবুক পেজ, গ্রুপ ও ট্রল অ্যাকাউন্টে বলা হচ্ছে, ফাহমিদা নাকি নির্বাচন বানচাল করতে চাইছেন। তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে “পতিত আওয়ামী লীগের এজেন্ট” আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সবচেয়ে ভয়াবহ হলো, তাঁকে গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং প্রকাশ্যে ট্যাগিং করে লজ্জাজনক ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে।এটাই হলো প্রোপ্যাগান্ডার সবচেয়ে বিপজ্জনক রূপ। যখন একজন নারী প্রার্থী নিজের সাংবিধানিক অধিকার ব্যবহার করে আদালতে যান, তখন তাকে ঘিরে এমন ভুয়া প্রচার চালানো হয় যাতে সমাজ তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এটি শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়; এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর আঘাত। এমন পরিস্থিতিতে সচেতন নাগরিক ও গণমাধ্যমের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু শিক্ষাঙ্গন নয়, বরং দেশের রাজনীতির উর্বর ক্ষেত্র। এখান থেকেই ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু একই সঙ্গে এখানে ছাত্র রাজনীতির নামে প্রোপ্যাগান্ডা, গুজব ও অপপ্রচারের দীর্ঘ ইতিহাসও রয়েছে। সত্তরের দশকে আওয়ামী ছাত্রলীগ ও জাসদের মধ্যে বিভক্তি তৈরি হয়েছিল মূলত প্রোপ্যাগান্ডার মাধ্যমে। আশির দশকে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালে শাসকগোষ্ঠী ছাত্রদের বিভ্রান্ত করতে নানা গুজব ছড়িয়েছিল। নব্বইয়ের গণআন্দোলনে প্রচুর পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল শুধু প্রোপ্যাগান্ডার অজুহাতে।
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোপ্যাগান্ডা শুধু ছাত্ররাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা হয়। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি, প্রতিপক্ষকে দুর্বল দেখানো এবং নির্বাচনী প্রচারণার মনস্তাত্ত্বিক কৌশল—সবই প্রোপ্যাগান্ডার অন্তর্ভুক্ত।
বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন হোক বা জাতীয় নির্বাচন—বাংলাদেশে নারী প্রার্থীরা সবসময়ই দ্বিগুণ চাপের মুখে পড়েন। একদিকে প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তাঁদের নেতৃত্বকে সন্দেহের চোখে দেখে, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তাঁদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়। এই সাম্প্রতিক ঘটনাতেও তাই ঘটছে। ফাহমিদা আলমের উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সংগঠনের প্রভাব রুখে দেওয়া। কিন্তু তাঁকে উল্টো “নির্বাচনবিরোধী” হিসেবে প্রোপ্যাগান্ডা চালানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে তাঁকে ভয় দেখানো, রাজনৈতিকভাবে একঘরে করা এবং মানসিকভাবে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।
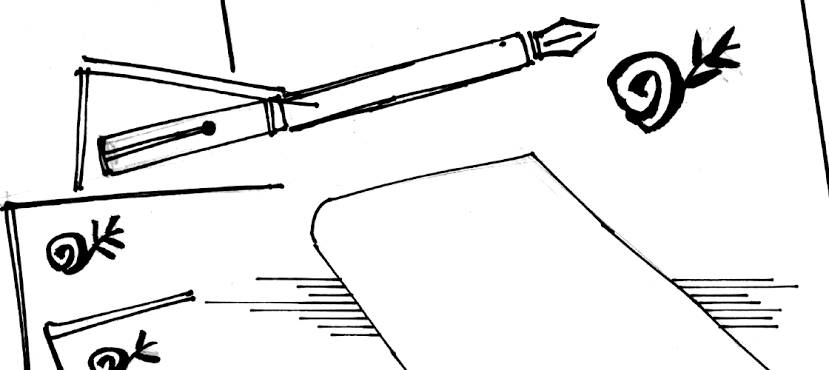 ডিজিটাল যুগে প্রোপ্যাগান্ডার বিস্তার দ্রুত ও ব্যাপক। ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, টিকটক—সব মাধ্যমে নকল ভিডিও, ফটোশপ করা ছবি এবং সংক্ষেপিত গল্প ছড়িয়ে পড়ছে। ভিডিও ক্লিপ বা মিমস যে কখন ভাইরাল হবে তা প্রেডিক্ট করা মুশকিল। বাংলাদেশের প্রায়ই দেখা যায়, কোনো রাজনৈতিক বিতর্কের প্রেক্ষিতে সামান্য সত্য তথ্যকে বিকৃতভাবে প্রচার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ফাহমিদা আলমের রিট কার্যক্রমকে বিভ্রান্তিকরভাবে উপস্থাপন করে তাকে “নির্বাচনবিরোধী” বা “সরকারি এজেন্ট” হিসেবে দেখানো হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ ভুল তথ্য বিশ্বাস করে এবং গণমাধ্যমের উপর আস্থা কমে যায়।ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের অ্যালগরিদমও প্রোপ্যাগান্ডার প্রসারকে সহায়তা করে। যে কোনো পোস্ট যত বেশি প্রতিক্রিয়া বা শেয়ার পায়, তা আরও বেশি মানুষের ফিডে আসে। এটি একটি ইতিবাচক ফিচার হলেও প্রোপ্যাগান্ডা ছড়ানোর জন্য ক্ষতিকর।প্রোপ্যাগান্ডার ব্যবহার শুধু বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ নয়। ইতিহাস এবং সাম্প্রতিক যুদ্ধ দেখিয়েছে, এটি বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উদাহরণে নাৎসি জার্মানি ও মিত্রশক্তি জনমতকে প্রভাবিত করতে পোস্টার, সিনেমা, রেডিও ব্যবহার করেছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালে মার্কিন প্রশাসন জনমত নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছিল। ইরাক যুদ্ধে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মিথ্যা দাবি এবং মিডিয়া প্রচারণা জনগণের মন ও আন্তর্জাতিক সমর্থনে প্রভাব ফেলেছিল। সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে দেখা যায়, যেখানে দুটি পক্ষই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং মিডিয়ার মাধ্যমে তথ্যযুদ্ধ চালাচ্ছে।এই আন্তর্জাতিক উদাহরণগুলি প্রমাণ করে যে, তথ্য ও মনস্তাত্ত্বিক কৌশল কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপটেও প্রোপ্যাগান্ডা ব্যবহারের প্যাটার্ন একই—তথ্য বিকৃতি, ভয়-ভীতি, এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার।প্রোপ্যাগান্ডা মোকাবেলায় নাগরিকদের সচেতনতা অপরিহার্য। তথ্য যাচাই, সমালোচনামূলক মনোভাব এবং সামাজিক দায়বোধই একমাত্র প্রতিরক্ষা। নাগরিক সচেতনতা শুধু ব্যক্তিগত সুরক্ষা নয়, বরং গণতান্ত্রিক সমাজ রক্ষার পথ।গণমাধ্যমের উচিত নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। বিকৃত খবর প্রচার করলে প্রোপ্যাগান্ডার হাতিয়ার শক্তিশালী হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেও নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রার্থীরা নিরাপদে প্রচারণা চালাতে পারেন। নারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে হুমকি বা অপপ্রচার থামানো আবশ্যক।প্রোপ্যাগান্ডা কেবল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের অস্ত্র নয়, এটি নাগরিক সচেতনতার পরীক্ষা। ফাহমিদা আলমের রিট ও ডাকসু নির্বাচন সংক্রান্ত বিতর্ক দেখিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমের প্রচারণা ও গুজব কত দ্রুত সমাজে প্রভাব ফেলতে পারে। নাগরিক, গণমাধ্যম এবং বিশ্ববিদ্যালয় সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে। সচেতনতা, তথ্য যাচাই, এবং সমালোচনামূলক মনোভাবই একমাত্র প্রতিরক্ষা। না হলে গণতান্ত্রিক সমাজের স্বচ্ছতা ও নারী নেতৃত্বের নিরাপত্তা হুমকির মুখে থাকবে।শুধু তথ্য ও বিচারকেন্দ্রিক নজর রাখলেই কাজ হবে না। শিক্ষার্থী, প্রার্থী, শিক্ষক, প্রশাসক এবং সাধারণ নাগরিক সবাইকে অংশ নিতে হবে। প্রোপ্যাগান্ডার মোকাবেলা মানে রাজনৈতিক সচেতনতা, সামাজিক দৃষ্টিকোণ, এবং নৈতিক দায়িত্বের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। এটি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে।ডাকসু নির্বাচনের এই ঘটনা আমাদের শেখাচ্ছে, প্রোপ্যাগান্ডা কেবল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে নয়, নাগরিক সমাজের সচেতনতা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা কমাতে ব্যবহৃত হয়। সামাজিক মাধ্যমের অজান্তে বা সচেতন ব্যবহারেই প্রভাব বিস্তার হয়। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং তথ্য যাচাই করা জরুরি।
ডিজিটাল যুগে প্রোপ্যাগান্ডার বিস্তার দ্রুত ও ব্যাপক। ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, টিকটক—সব মাধ্যমে নকল ভিডিও, ফটোশপ করা ছবি এবং সংক্ষেপিত গল্প ছড়িয়ে পড়ছে। ভিডিও ক্লিপ বা মিমস যে কখন ভাইরাল হবে তা প্রেডিক্ট করা মুশকিল। বাংলাদেশের প্রায়ই দেখা যায়, কোনো রাজনৈতিক বিতর্কের প্রেক্ষিতে সামান্য সত্য তথ্যকে বিকৃতভাবে প্রচার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ফাহমিদা আলমের রিট কার্যক্রমকে বিভ্রান্তিকরভাবে উপস্থাপন করে তাকে “নির্বাচনবিরোধী” বা “সরকারি এজেন্ট” হিসেবে দেখানো হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ ভুল তথ্য বিশ্বাস করে এবং গণমাধ্যমের উপর আস্থা কমে যায়।ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের অ্যালগরিদমও প্রোপ্যাগান্ডার প্রসারকে সহায়তা করে। যে কোনো পোস্ট যত বেশি প্রতিক্রিয়া বা শেয়ার পায়, তা আরও বেশি মানুষের ফিডে আসে। এটি একটি ইতিবাচক ফিচার হলেও প্রোপ্যাগান্ডা ছড়ানোর জন্য ক্ষতিকর।প্রোপ্যাগান্ডার ব্যবহার শুধু বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ নয়। ইতিহাস এবং সাম্প্রতিক যুদ্ধ দেখিয়েছে, এটি বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উদাহরণে নাৎসি জার্মানি ও মিত্রশক্তি জনমতকে প্রভাবিত করতে পোস্টার, সিনেমা, রেডিও ব্যবহার করেছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালে মার্কিন প্রশাসন জনমত নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছিল। ইরাক যুদ্ধে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মিথ্যা দাবি এবং মিডিয়া প্রচারণা জনগণের মন ও আন্তর্জাতিক সমর্থনে প্রভাব ফেলেছিল। সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে দেখা যায়, যেখানে দুটি পক্ষই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং মিডিয়ার মাধ্যমে তথ্যযুদ্ধ চালাচ্ছে।এই আন্তর্জাতিক উদাহরণগুলি প্রমাণ করে যে, তথ্য ও মনস্তাত্ত্বিক কৌশল কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপটেও প্রোপ্যাগান্ডা ব্যবহারের প্যাটার্ন একই—তথ্য বিকৃতি, ভয়-ভীতি, এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার।প্রোপ্যাগান্ডা মোকাবেলায় নাগরিকদের সচেতনতা অপরিহার্য। তথ্য যাচাই, সমালোচনামূলক মনোভাব এবং সামাজিক দায়বোধই একমাত্র প্রতিরক্ষা। নাগরিক সচেতনতা শুধু ব্যক্তিগত সুরক্ষা নয়, বরং গণতান্ত্রিক সমাজ রক্ষার পথ।গণমাধ্যমের উচিত নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। বিকৃত খবর প্রচার করলে প্রোপ্যাগান্ডার হাতিয়ার শক্তিশালী হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেও নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রার্থীরা নিরাপদে প্রচারণা চালাতে পারেন। নারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে হুমকি বা অপপ্রচার থামানো আবশ্যক।প্রোপ্যাগান্ডা কেবল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের অস্ত্র নয়, এটি নাগরিক সচেতনতার পরীক্ষা। ফাহমিদা আলমের রিট ও ডাকসু নির্বাচন সংক্রান্ত বিতর্ক দেখিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমের প্রচারণা ও গুজব কত দ্রুত সমাজে প্রভাব ফেলতে পারে। নাগরিক, গণমাধ্যম এবং বিশ্ববিদ্যালয় সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে। সচেতনতা, তথ্য যাচাই, এবং সমালোচনামূলক মনোভাবই একমাত্র প্রতিরক্ষা। না হলে গণতান্ত্রিক সমাজের স্বচ্ছতা ও নারী নেতৃত্বের নিরাপত্তা হুমকির মুখে থাকবে।শুধু তথ্য ও বিচারকেন্দ্রিক নজর রাখলেই কাজ হবে না। শিক্ষার্থী, প্রার্থী, শিক্ষক, প্রশাসক এবং সাধারণ নাগরিক সবাইকে অংশ নিতে হবে। প্রোপ্যাগান্ডার মোকাবেলা মানে রাজনৈতিক সচেতনতা, সামাজিক দৃষ্টিকোণ, এবং নৈতিক দায়িত্বের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। এটি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে।ডাকসু নির্বাচনের এই ঘটনা আমাদের শেখাচ্ছে, প্রোপ্যাগান্ডা কেবল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে নয়, নাগরিক সমাজের সচেতনতা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা কমাতে ব্যবহৃত হয়। সামাজিক মাধ্যমের অজান্তে বা সচেতন ব্যবহারেই প্রভাব বিস্তার হয়। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং তথ্য যাচাই করা জরুরি।
নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো শুধুমাত্র ভোট দেওয়া নয়। তথ্য যাচাই করা, সমালোচনামূলক মনোভাব বজায় রাখা, এবং প্রোপ্যাগান্ডার শিকার হওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করা। এটি রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের হাতিয়ার হতে পারে। সঠিক বিচার ও সচেতন মনোভাবই গণতান্ত্রিক সমাজকে টিকিয়ে রাখবে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক এই নির্বাচনের ঘটনাটি তাই শুধু শিক্ষাঙ্গনের ঘটনা নয়; এটি বাংলাদেশের গণতন্ত্র, তথ্যের স্বচ্ছতা এবং নাগরিক দায়বোধের ওপর এক বৃহৎ পরীক্ষা। প্রোপ্যাগান্ডার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে আমাদের প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে। ইতিহাস, সামাজিক দৃষ্টিকোণ এবং আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি—সব মিলিয়ে আমরা শুধু তথ্যের উপর নয়, মনস্তত্ত্বের উপরও নজর রাখতে হবে।
সর্বশেষে, ফাহমিদা আলমের রিট এবং ডাকসু নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে ঘটে যাওয়া প্রোপ্যাগান্ডা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, গণতন্ত্র শুধু ভোট কেন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি নাগরিক সচেতনতা, তথ্য যাচাই, সমালোচনামূলক মনোভাব এবং নারী নেতৃত্বের সুরক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। নাগরিক দায়বোধ ছাড়া, প্রোপ্যাগান্ডার এই নীরব যুদ্ধ সমাজকে বিভ্রান্ত এবং দুর্বল করতে পারে।
লেখক:সংবাদকর্মী

